গণতন্ত্রের সংজ্ঞা
গণতন্ত্রের কোনো সর্বজনীন সংজ্ঞা নেই। কেননা, কাল ও স্থানভেদে গণতন্ত্রের পার্থক্য ঘটে। সহজ ভাষায়, যেকোনো দুটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে ফারাক লক্ষ করা যায়। গণতন্ত্রের সংজ্ঞার প্রশ্নটি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে দীর্ঘদিন ধরেই আলোচিত ও বিতর্কিত। কয়েক দশক ধরে গণতন্ত্র ও গণতন্ত্রায়ণ-বিষয়ক গবেষণা, আলোচনা ও পর্যবেক্ষণে গণতন্ত্রের সংজ্ঞা ও গণতন্ত্রের প্রকৃতি নিয়ে ব্যাপকভাবে আলোচনা হয়েছে।
সমাজবিজ্ঞানে, বিশেষত রাষ্ট্রবিজ্ঞানে, গণতন্ত্রের অর্থ নিয়ে চিন্তাভাবনার মধ্যে দুটি প্রধান ধারা রয়েছে। এর একটি ধারায় গণতন্ত্রকে বিবেচনা করা হয় একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে, যা নির্দিষ্ট ‘নির্বাচনী’ ও ‘পদ্ধতিগত’ মানদণ্ড (বা নির্ণায়ক) অর্জনে সক্ষম হয়েছে। অন্য ধারাটিতে গণতন্ত্র ও গণতন্ত্রায়ণকে সমাজে কতগুলো সঠিক গণতান্ত্রিক ‘সাংস্কৃতিক’ উপাদান অর্জিত হওয়ার নিরিখে বিবেচনা করা হয়। পদ্ধতিগত গণতন্ত্রের ধারণার জনক জোসেফ সুম্পিটারকে বলা যেতে পারে। সুম্পিটারের ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত গ্রন্থ ক্যাপিটালিজম, সোশ্যালিজম অ্যান্ড ডেমোক্রেসি-এর (সুম্পিটার, ১৯৪৬/১৯৫০) লক্ষ্য হচ্ছে, গণতন্ত্র-সম্পর্কিত ‘অস্পষ্ট ধারণা’ থেকে সরে এসে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে পরিমাপ করা যায়, এমন সব সুস্পষ্ট নির্ণায়ক চিহ্নিত করা। তিনি গণতন্ত্রকে বর্ণনা করেন নেতৃত্ব নির্বাচনের ব্যবস্থা হিসেবে। সুম্পিটার লিখছেন:
The democratic method is that institutional arrangement for arriving at political decisions in which individuals acquire the power to decide by means of a competitive struggle for people's vote. (সুম্পিটার, ১৯৫০: ২৬৯)।
(গণতান্ত্রিক পদ্ধতি হচ্ছে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর এমন এক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, যেখানে জনগণের ভোট পাওয়ার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা লাভ করে।)
সহজ ভাষায় সুম্পিটারের কাছে গণতন্ত্র হলো, যারা সিদ্ধান্ত নেবে, তাদের নির্বাচনের ব্যবস্থা (সুম্পিটার, ১৯৫০: ২৯৬)। এই সংজ্ঞায় পদ্ধতিগত দিকটিই যে প্রাধান্য পেয়েছে, তা সহজেই লক্ষণীয়।
গণতন্ত্রের এই পদ্ধতিগত ধারণাকে রবার্ট ডাল তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ পলিয়ার্কি: পার্টিসিপেশন অ্যান্ড অপজিশন-এ বিস্তারিত ও সম্প্রসারিত করেন। ডাল যে ব্যবস্থার কথা তুলে ধরেন, সেটাকে তিনি বর্ণনা করেন ‘পলিয়ার্কি’ বা ‘বহুজনের শাসনব্যবস্থা’ হিসেবে। রবার্ট ডাল (১৯৭২) পদ্ধতিগত গণতন্ত্রের সুস্পষ্ট নির্ধারকের তাগিদ দিয়ে বলেন যে বহুজনের শাসনব্যবস্থার কতগুলো মৌলিক উপাদান রয়েছে। সেগুলো হলো: সরকারে সাংবিধানিকভাবে নির্বাচিত কর্মকর্তা থাকা; নিয়মিত, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন; সব পূর্ণবয়স্কের ভোটাধিকার এবং নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার অধিকার; মতপ্রকাশের স্বাধীনতা; সরকার বা কোনো একক গোষ্ঠীর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ রয়েছে এমন উেসর বিকল্প থেকে তথ্য পাওয়ার সুযোগ এবং সংগঠনের স্বাধীনতা। ডালের এই বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে বহুজনের শাসন হলো শাসনব্যবস্থার জন্য কতগুলো প্রতিষ্ঠান ও পদ্ধতির সমন্বিত রূপ। ডালের এই সংজ্ঞা বা বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে বিস্তর সমালোচনা থাকলেও এখন পর্যন্ত গণতন্ত্রের সংজ্ঞা ও গুণাগুণ বিচারে এগুলোই সবচেয়ে ব্যবহূত মাপকাঠি। সুম্পিটার ও ডালের এই মাপকাঠিকে গণতন্ত্রের পদ্ধতিগত (Procedural) এবং সবচেয়ে সীমিত (Minimalist) সংজ্ঞা বলা হয়ে থাকে।
পদ্ধতিগত এই সংজ্ঞার বিপরীতে অনেকেই সাংস্কৃতিক দিকে নজর দেওয়ার প্রয়োজনের ওপর জোর দেন। গত কয়েক দশকে অনেক দেশে সুষ্ঠু নির্বাচন সত্ত্বেও গণতন্ত্রের সমস্যা বিদ্যমান থাকার ফলে নির্বাচনভিত্তিক গণতন্ত্রের বদলে অন্যান্য কতিপয় বিষয়ের ওপর জোর দেওয়ার তাগিদ সৃষ্টি হয়। এই ধারণার প্রবক্তারা নাগরিকদের অধিকার, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও সিভিল সোসাইটি বা জনসমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণকে নির্ধারকের জায়গায় স্থান দেওয়ার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন। এঁদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন ল্যারি ডায়মন্ড (ডায়মন্ড, ১৯৯৩, ১৯৯৯, ২০০০, ২০০১, ২০০৮)। তিনি বলেন, নির্বাচনী গণতন্ত্রের (Electoral Democracy) ওপর গুরুত্বারোপের ফলে গণতন্ত্রের সাফল্যের ব্যাপারে যে বিভিন্ন ধরনের চিত্র রয়েছে, তা ঠিক বোঝা যায় না। তাই তিনি রাজনৈতিক সংস্কৃতি, সুশীল সমাজ ও গণতন্ত্রের বিভিন্ন ধরনের বিষয় বিবেচনায় নিতে বলেন। ডায়মন্ড ও অন্য গবেষকদের (যেমন: চ্যান্ডলার, ২০০০) দেওয়া গণতন্ত্রের সংজ্ঞাকে গণতন্ত্রের সম্প্রসারিত সংজ্ঞা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
গণতন্ত্র সম্পর্কে যেসব গবেষণা হয়েছে, তাকে আমরা আরও দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি। তা হলো: আদর্শিক (Normative) এবং ভূয়োদর্শনলব্ধ (Empirical)। প্রথম ধারা বলে গণতন্ত্র কেমন হওয়া উচিত, দ্বিতীয় ধারা ব্যাখ্যা করে কার্যত গণতন্ত্র কীভাবে কাজ করে। তা ছাড়া গণতন্ত্রের সীমিত সংজ্ঞা ও পরিবর্ধিত সংজ্ঞার পার্থক্যকে অনেকে ব্যাখ্যা করেন গণতন্ত্র একটি শাসনব্যবস্থা এবং গণতন্ত্র একগুচ্ছ মূল্যবোধ—এই দুই রকম দৃষ্টিভঙ্গির তফাত হিসেবে।
গণতন্ত্রসংক্রান্ত এই দুই ধরনের ধারণার সমন্বয়সাধনের চেষ্টা একেবারে হয়নি তা নয়, বরং অনেকের ধারণা, এই দুই ধারণার সমন্বয়েই আমরা কতগুলো নির্ণায়ক তৈরি করতে পারি, যা একটি দেশের গণতন্ত্রের গুণাগুণ বিচারে সাহায্য করতে পারে। এই সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গণতন্ত্রের তিনটি উপাদানকে মৌলিক বা বুনিয়াদি বলে বিবেচনা করা যায়। এগুলো হলো: ১. সর্বজনীন ভোটাধিকার; ২. আইনসভা ও নির্বাহী বিভাগের প্রধানের পদের জন্য নিয়মিত, অবাধ, প্রতিযোগিতামূলক, বহুদলীয় নির্বাচন; ৩. মতপ্রকাশ ও সংগঠনের স্বাধীনতাসহ সব ধরনের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের প্রতি সম্মান এবং আইনের শাসন, যার আওতায় রাষ্ট্রের প্রতিনিধি ও নাগরিক আইনিভাবে প্রকৃত অর্থেই সমানভাবে বিবেচ্য। এই বৈশিষ্ট্যগুলোর একটি পক্ষপাত সীমিত সংজ্ঞার প্রতি থাকলেও, এটা জোর দিয়ে বলা আবশ্যক যে এই তিনটি উপাদান পরস্পর সংশ্লিষ্ট। অর্থাত্ স্বতন্ত্রভাবে এর একটি উপাদানের সাফল্য গণতন্ত্রের আংশিক সাফল্যের পরিচায়ক নয়। গণতন্ত্রের জন্য এই তিনটি উপাদানকে সমভাবে কার্যকর থাকতে হবে এবং সাফল্য লাভ করতে হবে। তা ছাড়া এই উপাদানগুলোকে চূড়ান্ত লক্ষ্য বলে বিবেচনা করা যাবে না; বিবেচনা করতে হবে গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে।

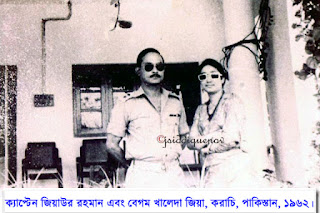


Comments